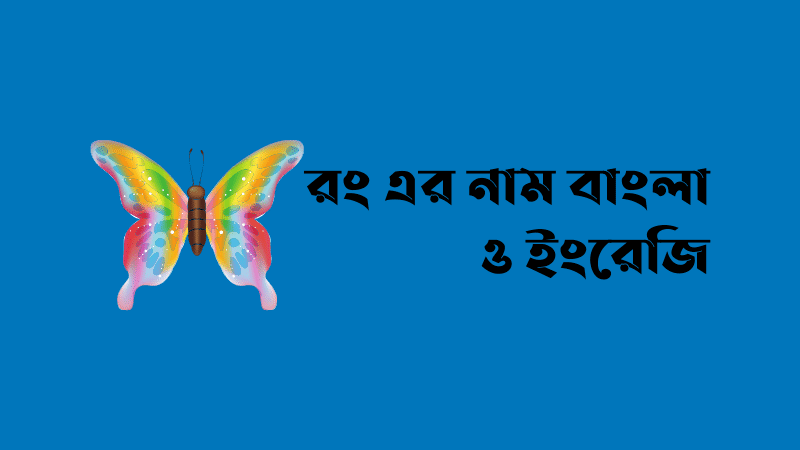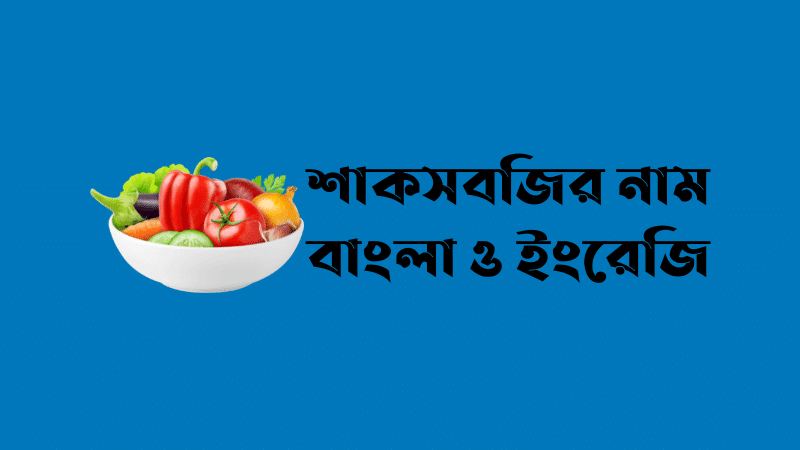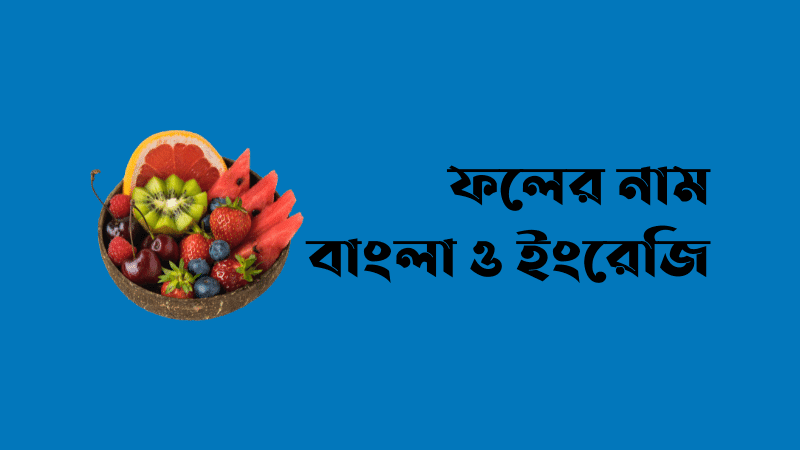চোখের যত্নে চশমা কি জরুরি
চোখের প্রয়োজনীয়তা
নিম্নতর প্রাণীদের অধিকাংশের চোখ তেমন সুগঠিত নয়। তাই তাদের অনেকের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তির চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়। কিন্তু কোন একটি পর্যায়ে মানবসদৃশ প্রাণীদের এক দলের ক্ষমতা জন্মায় দু’চোখের দৃষ্টি একই বস্তুতে নিবদ্ধ করার; তার ফলে সম্ভব হয় উন্নত ত্রিমাত্রিক দৃষ্টি। এই এই ত্রিমাত্রিক দৃষ্টির কল্যাণে তাদের পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর তাই আজ মানুষের কাছে চোখ হয়ে উঠেছে এমন দামী যে, আমরা বলি ‘একবার দেখা এক শ-বার শোনার চেয়ে ভাল’ কিংবা সবচেয়ে প্রিয়বস্তুর তুলনা করি চোখের মণির সাথে।
চোখ যে শুধু আমাদের প্রয়োজনের অঙ্গ তা নয়, রূপেরও অঙ্গ। সুন্দর চোখের রূপবর্ণনায় কবি-সাহিত্যিকরা ক্লান্তিহীন। কালো ভ্রমর, চেরা পটল, অতল দীঘি, পাখির নীড়, নৃত্যপরা হরিণী—এসব কোন কিছুরই উপমা চোখের জন্য বাদ পড়েনি। কিন্তু চোখ পটলচেরা হোক বা না হোক, তার মণি হোক কাজল-কালো অথবা নীল, কটা, সোনালী বা ধূসর - সব চোখের কাজ একই। সে হল চারপাশের প্রকৃতির একটি তথ্যপূর্ণ, সত্যনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি মানুষের মনে এঁকে দেওয়া।
চোখের কাজ
এই যে দেখা বা মনের ওপর প্রকৃতির ছাপ ফেলার ক্ষমতা, এ কিন্তু চোখ আমাদের জন্মের সাথে সাথে আপনা-আপনি আয়ত্ত করে না।
আমাদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অনেকটাই গড়ে ওঠে জন্মের পরে ধীরে ধীরে প্রকৃতির সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। চারপাশের নানা বস্তুর দূরত্ব, গড়ন, এক থেকে অন্যের পার্থক্য এসব আমরা বুঝতে পারি মূলত দৃষ্টির মাধ্যমে। বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও গভীরতা এই উপলব্ধির সহায়ক হয়। বাইরের পরিবেশে কোন পরিবর্তন ঘটলে তাও দৃষ্টির মাধ্যমেই সবচেয়ে দ্রুত আমাদের অনুভূতিতে সাড়া জাগায়।
তবে বাইরের প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে যায় তার সবই যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে মনে সমান সাড়া সৃষ্টি করে তা নয়। আসলে চোখের মাধ্যমে দেখে আমাদের মস্তিষ্ক। দৃশ্যবস্তুর আলো পড়ে চোখের পেছনের পর্দা রেটিনা বা অক্ষিপটে যে ছাপ ফুটে ওঠে তা স্নায়ু সংযোগের মাধ্যমে মস্তিষ্ককোষে সাড়া জাগায়। এমনি অসংখ্য সাড়ার মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো তথ্যগুলো মস্তিষ্ক বাছাই করে নেয়। এজন্য দেখার প্রক্রিয়ায় চোখ আর মস্তিষ্কের সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
দৃষ্টিশক্তি সহায়ক বস্তু
দীর্ঘকাল ধরে মানুষ চেষ্টা করে আসছে তার দৃষ্টিশক্তিকে বাড়াতে, দৃষ্টি পরিধি আরো প্রসারিত করতে। দৃষ্টির বিভিন্ন ত্রুটি দূর করার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে চশমা। নানা জটিল পরিস্থিতিতে কাজের জন্য তৈরি হয়েছে দৃষ্টি সহায়ক অসংখ্য উপকরণ। নানা ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র মানুষের দৃষ্টিকে নিয়ে গিয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুজীবের জগতে। দূরবীন যন্ত্র আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর করেছে মহাকাশের অনেক গোপন তথ্য। সাগরের গভীর তলে বা বস্তুর গহন কন্দরে আজ মানুষের দৃষ্টিসীমা প্রসারিত।
আরও পড়তে পারেনঃ হৃদরোগ কী, কেন হয়?
চোখের গঠন
প্রকৃতির দিক দিয়ে শুধু যে নানা বর্ণ আর গোত্রের মানুষের চোখের প্রকৃতিতে মিল আছে তা নয়। মানুষের চোখের সাথে পাখি, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি অন্যান্য প্রজাতির প্রাণীদের চোখের গড়নেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। মানুষের চোখ মাথার সামনে অক্ষিকোটরে বসানো মোটামুটি ২৪ মি. মি. ব্যাসের প্রায় বর্তুলাকার একটি বস্তু। এর ওপরের মজবুত আবরণটির সামনের দিক দেখতে অনেকটা চকচকে সাদা চীনামাটির মতো। তার মাঝখানের অপেক্ষাকৃত উঁচুতেও স্বচ্ছ অংশটিকে বলা হয় কর্নিয়া বা অচ্ছোদপটল—এখান দিয়েই বাইরের দৃশ্যের আলো ঢোকে চোখে। কর্নিয়ার তলায় রয়েছে মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত একটি কালো গোল স্তর। এটিই হল চোখের তারা বা মণি।
চোখের তারার রঙ আমাদের দেশে সচরাচর কালো হলেও কটা, নীল, সবুজ ইত্যাদি আরো নানা রঙের চোখ দেখতে পাওয়া যায়। রঙের জন্য চোখের দৃষ্টিশক্তিতে কোন তারতম্য হয় না তবে তারার রঙ যে নারী বা পুরুষের রূপের অঙ্গ তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য রূপ সঞ্চারের চেয়েও বড় কাজ রয়েছে তারার। সে হল বিভিন্ন রকম আলোর তীব্রতায় চোখকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করা। অন্ধকার ঘরে তারার আকার হয়ে যায় শিশুর আঙুলের আংটির মতো, আর তার মাঝখানের ফুটো হয়ে ওঠে বড়। আবার কড়া আলোয় ফুটোটা চুপসে হয়ে যায় ছোট। বিজ্ঞানীরা মেপে দেখেছেন, দিনের উজ্জ্বল আলোয় এই ফুটো বা তারারন্ধ্রের ব্যাস হতে পারে মাত্র ২ মিলিমিটার। আবার অন্ধকারে এই মাপ বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৮ মিলিমিটার। ব্যাপারটা অনেকটা ক্যামেরার অ্যাপারচার ছোট-বড় করার মতো, তবে আমাদের মস্তিষ্ক এই খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারটা অনবরত করে যাচ্ছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।
তারার পেছনে আছে একটি উভ-উত্তল স্বচ্ছ লেন্স—চারপাশে গোল মাংসপেশীর সাথে আটকানো। লেন্সটির গড়ন আসলে বেশ জটিল—পরতে পরতে বেশ ক’টি লেন্সের সমাবেশ। এই লেন্সের ভেতর দিয়ে বাইরের দৃশ্যের আলো ঢুকে চোখের পেছনের দেয়াল বা রেটিনার ওপর পড়ে একটি ওল্টানো প্রতিচ্ছবি—ঠিক যেমন পড়ে ক্যামেরার ফিল্মের ওপর।
রেটিনার গায়ে রয়েছে দু’ধনের অতি সূক্ষ্ম আলোকসংবেদী কোষ। তাদের এক জাতকে বলা হয় ‘রড’ বা দণ্ড - এরা সাদা-কালো রঙ এবং বিশেষ করে কম আলোতে দেখতে সাহায্য করে। অন্য জাতকে বলা হয় ‘কোণ’ বা শঙ্কু—এরা রঙিন জিনিস এবং বিশেষ করে দিনের আলোয় দেখতে সাহায্য করে। মানুষের চোখে দণ্ডকোষ আছে প্রায় তের কোটি, সে তুলনায় শঙ্কুকোষের সংখ্যা অনেক কম—মাত্র সত্তর লাখের মতো। দণ্ডকোষগুলো ছড়ানো সারা রেটিনাজুড়ে। তবে শঙ্কুকোষেরা থাকে প্রধানত ‘হলদে ছোপ’ নামে রেটিনার মাঝামাঝি বিশেষ এলাকায়। এই প্রায় চৌদ্দ কোটি সংবেদী কোষ মগজের সাথে জোড়া আছে প্রায় দশ লাখ স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে। ‘হলদে ছোপ’ এলাকায় স্নায়ুতন্তুর সমাবেশ ঘন, তাই এখানে প্রতিচ্ছবি পড়লে সে দৃশ্য সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। রেটিনায় পড়া উল্টো প্রতিচ্ছবি মগজ আপনা-আপনি সোজা করে নিয়ে আমাদের বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দৃশ্য দেখায়।
চোখের দৃষ্টির উপযোজন
ক্যামেরায় কোন দৃশ্যের ছবি তুলতে হলে আগে দৃশ্যটি বাছাই করে সেদিকে বাগিয়ে ধরতে হয় লেন্স। তারপর দৃশ্যের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাবার জন্য লেন্স ফোকাস করতে হয়। ক্যামেরা ফোকাস করার জন্য লেন্স সামনে পেছনে করার ব্যবস্থা থাকে। দৃশ্যটা যখন বেশ দূরের হয়ে তখন লেন্স থাকে পেছনের ফিল্মের সব চাইতে কাছে। আবার কাছের ছবি নিতে হলে লেন্সকে এগিয়ে দিতে হয় সামনে। চোখের বেলাতেও দেখার জন্য দূরের বা কাছের বস্তুর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। সুঁই-এর মাথায় সুতো পরাবার সময় সুঁইটা চোখ থেকে দশ-পনের সেন্টিমিটার দূরে রাখলে ফুটো সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। আবার যখন আমরা পূর্ণিমার চাঁদ দেখি তখন তার সে আলো প্রায় চার লাখ কিলোমিটার দূরের। চারপাশের নানা দৃশ্য থেকে মস্তিষ্ক স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনমতো দৃশ্য বেছে নেয় আর চোখকে নিয়ন্ত্রণ করে দৃশ্যের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি রেটিনার ওপর ফেলে। বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ প্রবাহের পরীক্ষা থেকে দেখেছেন কোন প্রাণী যখন প্রথম কোন নতুন দৃশ্য বা নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন মস্তিষ্কের ব্যাপক এলাকাজুড়ে আলোড়ন শুরু হয়। কিন্তু একই অভিজ্ঞতা বারবার ঘটতে থাকলে ক্রমে ক্রমে মস্তিষ্কের অল্প অংশে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মস্তিষ্কের স্নায়ু সংযোগের দক্ষতা বাড়ে। ক্যামেরার সাথে চোখের একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, চোখে ‘ফোকাসিং’ ঘটে লেন্স আগে-পিছে করে নয়, লেন্সের বক্রতা কমিয়ে বাড়িয়ে। বিভিন্ন দূরত্বের নানা দৃশ্যের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তৈরির এই ব্যবস্থাটিকে বলা হয় দৃষ্টির উপযোজন (accommodation)। দূরের দৃশ্য দেখার সময় চোখের লেন্সের বক্রতা থাকে সবচেয়ে কম অর্থাৎ ফোকাস দূরত্ব হয় বেশি। কাছের দৃশ্য দেখার জন্য ফোকাস দূরত্ব কমাতে হয়। মস্তিষ্কের স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ও চারপাশের পেশীর চাপে লেন্সের বক্রতা প্রয়োজনমতো বাড়ে। এই পদ্ধতি কাজে লাগানো যায় এমন স্থিতিস্থাপক বস্তুর লেন্স মানুষ আজও তৈরি করতে পারেনি।
আরও পড়তে পারেনঃ মানুষের ঘুম পায় কেন?
দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে চোখের উপযোজনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বয়োবৃদ্ধি বা আর কোন কারণে চোখের উপযোজনের ক্ষমতা কমে গেলে দেখা দেয় দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি। এসব ত্রুটি দূর দূর করার জন্য মনে হয় মানুষ স্বচ্ছ পাথর ব্যবহার করেছে কয়েক হাজার বছর আগেও। একাদশ শতকে পড়বার জন্য এমনি দৃষ্টি সহায়ক পাতলা পাথরের খণ্ড চোখের কাছে ধরার কথা জানা যায়। ১২৭০ খ্রিস্টাব্দে লেখা মার্কোপোলোর বিবরণে পাওয়া যায়, চীন দেশে সেকালে বৃদ্ধ লোকেরা ছোট হরফের লেখা পড়বার জন্য উত্তল পরকলা ব্যবহার করত। প্রায় এ সময়েই রোজার বেকন উল্লেখ করেছেন কাচ বা এ জাতীয় বস্তুর সাহায্যে লেখা বড় দেখাবার কথা। নাকের ওপর বসানো চশমা সম্ভবত প্রথম তৈরি হয় ইতালিতে। একই চশমায় দু’রকম কাচ ব্যবহার করে ‘বাই ফোকাল’ তৈরির রেওয়াজ চালু করেন আমেরিকায় বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন-অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।
দৃষ্টিশক্তি ত্রুটি
দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি হয় প্রধানত দু’ধরনের। এক হল দূরবদ্ধ দৃষ্টি; এতে চোখের লেন্সের বক্রতা প্রয়োজনমতো বাড়ানো যায় না। তাই দূরের দৃশ্য মোটামুটি দেখা যায়, কিন্তু কাছের বস্তু দেখার ঝাপসা। আরেক সমস্যা হল নিকট দৃষ্টি এতে লেন্সের বক্রতা প্রয়োজনমতো কমানো যায় না। তাতে কাছের জিনিস দেখায় ভাল। দূরের জিনিসের বেলায় ঘটে অসুবিধে। অষ্টাদশ শতকের চক্ষু চিকিৎসকরা মনে করতেন এসব সমস্যার প্রকৃত কোন প্রতিকার নেই। যদিও বয়স বাড়লে দূরবদ্ধ দৃষ্টি আপনা-আপনিই সেরে যেতে পারে। তো সাময়িক স্বস্তির জন্য তাঁরা দূরবদ্ধ দৃষ্টির ক্ষেত্রে উত্তল দর্পণ (আয়না বা কাঁচ) আর নিকট দৃষ্টির ক্ষেত্রে অবতল দর্পণ ব্যবহারের ব্যবস্থা দিতেন।
উনিশ শতকের বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে বললেন, এসব ত্রুটির প্রধান কারণ হল চোখের লেন্সের এবং লেন্সকে ধারণ করে থাকে যেসব পেশী তাদের স্থিতিস্থাপকতা কমে যাওয়া। লেন্স আর রেটিনার দূরত্ব বেশি হলে অর্থাৎ চোখ সামনে পেছনে বেশি লম্বা হলে দেখা দেয় নিকটদৃষ্টি, আর চোখ স্বাভাবিক আকারের চেয়ে খাটো হলে সৃষ্টি হয় দূরবদ্ধ দৃষ্টি।
উনিশ শতকের শেষদিকে চক্ষু চিকিৎসকরা দেখলেন দূরবদ্ধ দৃষ্টি বা নিকট-দৃষ্টি দুইই আসলে হতে পারে নানা ধরনের, আর এসবের কারণও হতে পারে বিভিন্ন। যেমন নিকট-দৃষ্টি দেখা দিতে পারে কর্নিয়া অতি-উত্তল হবার কারণে, চক্ষু গোলক বেশি লম্বা হলে, চোখের লেন্সের সামনের দিক অতি উত্তল হলে, কর্নিয়া অথবা চক্ষুরস বেশি ঘন হলে কিংবা তার রন্ধ্র অতি প্রশস্ত হলে। তেমনি দূরবদ্ধ দৃষ্টির কারণের মধ্যে রয়েছে কর্নিয়া বেশি চ্যাপটা হওয়া, চক্ষুগোলক খাটো হওয়া, লেন্সের সম্মুখ-বক্রতা কম হওয়া, কর্নিয়া বা চক্ষুরসের ঘনত্ব কম হওয়া অথবা তারা রন্ধ্র অতি সঙ্কুচিত হওয়া।
১৯২০ সালে নিউইয়র্কে উইলিয়ম বেটস (William Bates) নামে নামে একজন চক্ষু চিকিৎসক একটি বই প্রকাশ করেন - তার নাম “বিনা চশমায় নিখুঁত দৃষ্টি”। ১৯৬৭ সালে বইটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই বইতে দৃষ্টির বিভিন্ন ত্রুটির কারণ এবং সে সবের সংশোধন সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা নিয়ে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এসব প্রশ্ন তখন থেকেই বিশেষজ্ঞদের জন্য নানা চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে।
দৃষ্টিহীনতার কারণ
আসলে চোখের ভেতরে আলোর প্রতিসরণ ঘটে চারটি মাধ্যমে। (১) কর্নিয়া, (২) কর্নিয়া ও লেন্সের মধ্যবর্তী জলীয় রস, (৩) লেন্স এবং (৪) লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী আঠালো রস। এদের মধ্যে পেশী সংকোচনের মাধ্যমে বক্রতা বদলানো যায় শুধু লেন্সের গায়ের।
আদিকালে মানুষ ছিল মূলত শিকারি, পশুপালক, কৃষিজীবী অথবা যোদ্ধা; এদের সবারই চোখ ব্যবহৃত হত প্রধানত দূরের জিনিস দেখার জন্য। এটা চোখের স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, কেননা এ অবস্থায় চোখ দূরের জিনিস দেখার জন্য ফোকাস করা থাকে। কাজেই সেকালে মানুষের চোখের পেশী সংকোচনের প্রয়োজন খুব কমই হত। কাছের জিনিস দেখার জন্য চোখের উপযোজনের দরকার কখনো হলেও সে হত অতি সাময়িকভাবে আর স্বল্পকালের জন্য।
বেটস পরীক্ষা করে দেখলেন নিকট-দৃষ্টি ত্রুটির উদ্ভব কাছের জিনিস দেখার সমস্যা থেকে নয়, বরং দূরের জিনিস দেখার জন্য চোখের ওপর চাপের ফলে, আর দূরবদ্ধ দৃষ্টি হয় কাছের জিনিস দেখার জন্য চোখের ওপর অতিরিক্ত চাপ থেকে। তিনি বললেন, চোখের দৈর্ঘ্য কম হলে দূরদৃষ্টি বা বেশি হলে নিকট-দৃষ্টি ঘটবে এই ব্যাখ্যা মেনে নেয়া যায় না। তেমনি চোখে আলোক-প্রতিসরণের ত্রুটির জন্য দায়ী চক্ষুপেশীর মোটামুটি স্থায়ী সংকোচন এবং তার ফলে চক্ষু লেন্সের বক্রতার অবস্থা এ ব্যাখ্যাও মেনে নেয়া শক্ত। আসলে চোখের আলোক-প্রতিসরণের বিকৃতি প্রায়ই স্থায়ী অবস্থা নয়; অল্প মাত্রায় ঘটলে তা দূর করা সম্ভব, আর বেশি মাত্রায় ঘটলেও এ ত্রুটি কমানো যায়। চোখের আলোক প্রতিসরণ মাপবার জন্য রেটিনোস্কোপ যন্ত্রের ব্যবহার বেটসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ সহায়ক হল। এর আগে শুধু চোখের সামনে লেখাযুক্ত কার্ড রেখে এবং নানা মাপের লেন্স রদবদল করে প্রতিসরণের মাপ নেওয়া যেত। রেটিনাস্কোপ যে কোন প্রাণীর স্থির অথবা চলন্ত অবস্থায় প্রতিসরণের তাৎক্ষণিক এবং সঠিক মাপ নেয়া সম্ভব করে তুলল। বেটস মানুষ ছাড়াও বেড়াল, খরগোশ, ঘোড়া, পাখি, কচ্ছপ, মাছ প্রভৃতি অসংখ্য প্রাণীর চোখের প্রতিসরণ এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলেন; পরীক্ষা করলেন শত শত শিশু, কিশোর ও বয়স্ক ব্যক্তির চোখ-স্থির ও চলন্ত অবস্থায়, দিনে ও রাতে, জেগে থাকা এবং ঘুমন্ত অবস্থায়।
এসব পরীক্ষা থেকে তাঁর কাছে মনে হল আসলে চোখের উপযোজনে লেন্সের কোন ভূমিকা নেই। আর সুস্থ, স্বাভাবিক চোখ সর্বক্ষণই স্বাভাবিক দৃষ্টির অধিকারী এবং আলোক প্রতিসরণের ত্রুটির জন্য দায়ী অক্ষিগোলকের স্থায়ী বিকৃতি এমন সব ধারণাও ঠিক নয়। তিনি বললেন, আসলে অক্ষিগোলকের আকার নিয়ন্ত্রণ করে চোখের চারপাশের নিয়ন্ত্রক পেশী আর এই আকার কোন অবস্থাতেই স্থির নয়, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। আসলে খুব কম লোকের চোখের দীর্ঘকাল স্বাভাবিক দৃষ্টি বজায় থাকে; চোখের পেশীর আকুঞ্চন-বিকুঞ্চনের ফলে সর্বক্ষণই তাতে ঘটছে পরিবর্তন। তরুণ বা বৃদ্ধ কারো দৃষ্টিশক্তিই একনাগাড়ে কয়েক মিনিটের বেশি সময় স্বাভাবিক থাকে না। বিশেষ করে অপরিচিত কোন জিনিস দেখলে সাথে সাথে চোখের প্রতিসরণে পরিবর্তন ঘটা প্রায় অবধারিত।
ঘুমন্ত অবস্থাতেও মানুষের দৃষ্টিশক্তি কদাচিৎ স্বাভাবিক থাকে। জেগে থাকা অবস্থায় যাদের দৃষ্টি স্বাভাবিক তাদেরও ঘুমন্ত অবস্থায় চোখ হতে পারে দূরবদ্ধ, নিকটবদ্ধ বা বক্রদৃষ্টি। চোখে যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহলে তা ঘুমন্ত অবস্থায় বেড়ে যেতে পারে। বেটস বললেন, এজন্যই অনেকে সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠলে তাদের চোখ থাকে ক্লান্ত, কখনো তার সাথে থাকে তীব্র মাথাব্যথা।
অনেক সময় দেখা যায় জ্বরজাতীয় অসুখের পর ছোট ছেলেমেয়েদের নিকট-দৃষ্টির ত্রুটি দেখা দেয়। জীবজন্তুর ওপর পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে একই সাথে দেহে উচ্চ তাপমাত্রা এবং চোখে চাপ প্রয়োগের ফলে অল্পবয়স্ক প্রাণীদের নিকট-দৃষ্টি সৃষ্টি হয়। কিন্তু বয়স্ক প্রাণীদের বেলায় তা হয় না। চোখের লেন্সের স্থিতিস্থাপক গুণ সম্পর্কে সাম্প্রতিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, এই স্থিতিস্থাপকতা বয়সের সাথে সাথে কমতে থাকে, তার ফলে উপযোজনের ক্ষমতায় ঘাটতি দেখা দেয়। আগেই বলা হয়েছে লেন্সের আকার বেশ জটিল এবং আসলে এতে রয়েছে স্তরে স্তরে কতকগুলো লেন্সের সমষ্টি। তার মধ্যে ভেতরের লেন্সের বস্তুর দৃঢ়তা বেশি; বয়সের সাথে সাথে এই দৃঢ়তা বাইরের স্তরগুলোতেও বিস্তৃত হতে থাকে। কাজেই চারপাশের পেশীর পক্ষে লেন্সকে নমিত করে প্রয়োজন মতো উপযোজন ঘটানো ক্রমেই শক্ত হয়ে ওঠে।
এর ফলে কি বেটসের তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে? তা হয়তো নয়। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চোখের প্রকৃতি এবং তার ত্রুটি সংশোধনের উপায় সম্পর্কে কতকগুলো মূল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
চশমা ব্যবহার কতটা নিরাপদ?
দেহের অন্যান্য সংবেদী ইন্দ্রিয় থেকে চোখের একটি পার্থক্য এই যে, চোখের রেটিনার উদ্ভব আদি ভ্রূণের কেন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে। সেদিক থেকে গঠনগতভাবে রেটিনাকে বলা যেতে পারে মস্তিষ্কেরই বহিরঙ্গ। তাহলে চোখের দৃষ্টি ত্রুটি আসলে হয়তো মস্তিষ্ক বা মনের কোন অস্বাভাবিক অবস্থার প্রকাশমাত্র। অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসার লক্ষ্য হল রুগণ অবস্থার প্রতিকার করে দেহযন্ত্রকে আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির ত্রুটির জন্য চশমা ব্যবহার করা হলে আসলে চোখকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা না করে বরং তাকে তার বিকৃত অবস্থায় রেখে দেবারই স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়। চোখের সামনে একজোড়া স্বচ্ছ কাচ বসিয়ে দেবার ফলে তার আগের অবস্থায় ফিরে যাবার আর কোন পথ খোলা থাকে না। বেটস বলছেন, চশমা আদৌ ব্যবহার না করলে হয়তো বা এই ত্রুটি স্থায়ী হত না, কেননা কখনো হঠাৎ কারো চশমা ভেঙে গেলে যদি তাকে চশমাবিহীন কদিন কাটাতে হয় তাহলে প্রায়ই দেখা যায় তার দৃষ্টিশক্তির আপনা-আপনি কিছুটা উন্নতি ঘটেছে।
বয়স বা অন্য কারণে চোখের লেন্সের বা অন্য অংশের গঠনগত ত্রুটি ঘটা খুবই সম্ভব। কিন্তু তার জন্য ঘন ঘন চশমা বদলানোই কি একমাত্র সমাধান? অনেক ক্ষেত্রেই চোখের দুর্বলতার রোগীর আসল প্রয়োজন হয়তো নতুন দু’টি লেন্সের নয়, জগৎ সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির। অসুস্থ সমাজ ও পরিবেশ জন্ম দেয় অসুস্থ মনের; তার চিকিৎসা শুধু চশমা বদল করে হওয়া সম্ভব নয়। বরং চশমা যত কম ব্যবহার করে এবং যত কম বদলে দৃষ্টির সুস্থতা রক্ষা করা যায় সেটাই হওয়া উচিত চিকিৎসাবিদ্যার লক্ষ্য।
কিন্তু এই লক্ষ্য বাস্তবে কার্যকর হওয়া দুরূহ। চশমা আজ শুধু দৃষ্টিসহায়ক নয়, অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গের ভূষণ; দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা মানুষের অভ্যাস বা রুচি বদলানোও শক্ত। তার ওপর অসংখ্য চশমা প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী আর চক্ষু চিকিৎসকের পেশার প্রশ্ন এর সাথে জড়িত। তাই এ ধরনের বক্তব্য সহজেই যে সকলে গ্রহণ করবেন তা আশা করা শক্ত। তবু চশমার ব্যাপক সমাহার নয়, চশমাবিরল সমাজই কি আমাদের কাম্য হতে পারত না?